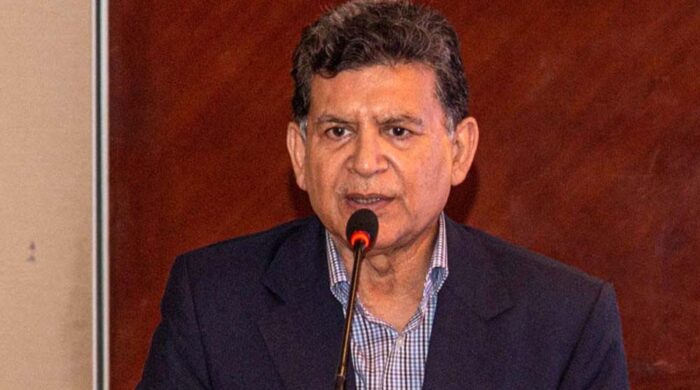
প্রভাত রিপোর্ট: ধীরগতির প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ খরাসহ নানা কারণে দেশে কর্মসংস্থান সংকট মহামারী আকার ধারণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিশিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, দেশে কর্মসংস্থান সংকটের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষার অভাব এখন প্রকট। আমরা শিক্ষা ও শিখন উভয় ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছি। মানসম্মত শিক্ষার অভাবেও তরুণরা চাকরি পাচ্ছে না।
শনিবার পিপিআরসি আয়োজিত ‘হোয়াট ইজ ড্রাইভিং দ্য পভার্টি রিভার্সেল ইন বাংলাদেশ?’ শীর্ষক এক অনলাইন সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে পিপিআরসির করা গবেষণার অর্থনৈতিক নানা দিক তুলে ধরেন হোসেন জিল্লুর রহমান। গবেষণায় দেখা যায়, দেশে দারিদ্র্যের হার ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ১০ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সালে দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা ১৮ শতাংশ মানুষ এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর অন্যতম কারণ কভিড-১৯, মূল্যস্ফীতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধির পেছনে মূল কারণ হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা। গবেষণায় দেখা গেছে, ৫১ শতাংশ পরিবারে কমপক্ষে একজন দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ রোগী। ৪০ শতাংশ মানুষের ঋণ ক্রমাগত বাড়ছে।
১২ শতাংশ দরিদ্র পরিবার খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। গবেষণায় আরো দাবি করা হয়, দেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ এখনো স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি বিবেচনায় ৩৮ শতাংশ লোক কর্মহীন। ৪৫ শতাংশ মানুষ আত্মকর্মসংস্থানে রয়েছে।
সংলাপে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন, ‘দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে অনেক বেশি। যেটি ২০২১-২২-এর প্রতিবেদনে সেভাবে আসেনি। দারিদ্র্য দূরীকরণে অন্যান্য সরকারের মতো অন্তর্বর্তী সরকারও তেমন পদক্ষেপ নেয়নি। এ সরকারের প্রধান কাজ হওয়া উচিত দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসে পদক্ষেপ নেওয়া, অন্তত ১৮-২৪ মাসের জন্য। অথচ এখন পর্যন্ত কোনো সংস্কার এজেন্ডায় দারিদ্র্য, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বিবেচনা হয়নি।’
সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, ‘গত কয়েক দশকে আমরা যে উন্নয়ন মডেল দেখেছি, সেটি তথাকথিত ‘চাকরিহীন প্রবৃদ্ধি’ তৈরি করেছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি দশকেই আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন্তত ১ শতাংশ হারে বেড়েছে, কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার তাল মেলাতে পারেনি। ফলে কর্মসংস্থান এখন একটি সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থান আসবে কোথা থেকে? বিনিয়োগ থেকে। অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জিডিপির ২৩-২৪ শতাংশে আটকে আছে, আর বৈদেশিক বিনিয়োগ জিডিপির ১ শতাংশেরও কম। এত কম বিনিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আশা করা যায় না। সরকারি খাত সামান্য কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করছে, কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য।’
ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক ইমরান মতিন বলেন, ‘কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরেকটি শঙ্কার বিষয় নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জরিপে দেখা গেছে, বিশেষ করে শহুরে নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ কমেছে। গ্রামীণ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ আসলে একটি প্রকৃত চিত্র দেয় না, কারণ সেখানে অনেকটা পারিবারিক কৃষিকাজ ধরা হয়। মূল উদ্বেগের জায়গা হলো শহুরে নারীদের অংশগ্রহণ, যা কয়েক বছর ধরে স্থবির হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে হ্রাস পেয়েছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, ‘এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্যের একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সেজন্য মানসম্মত প্রতিষ্ঠাগুলোকে সংস্কার করতে হবে।’
সংলাপে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমএ সাত্তার মন্ডলসহ অর্থনীতিবিদ, গবেষক, অ্যাক্টিভিস্টরা ভার্চুয়ালি অংশ নেন।